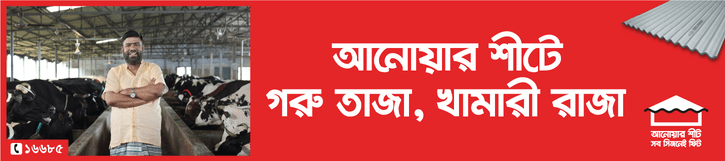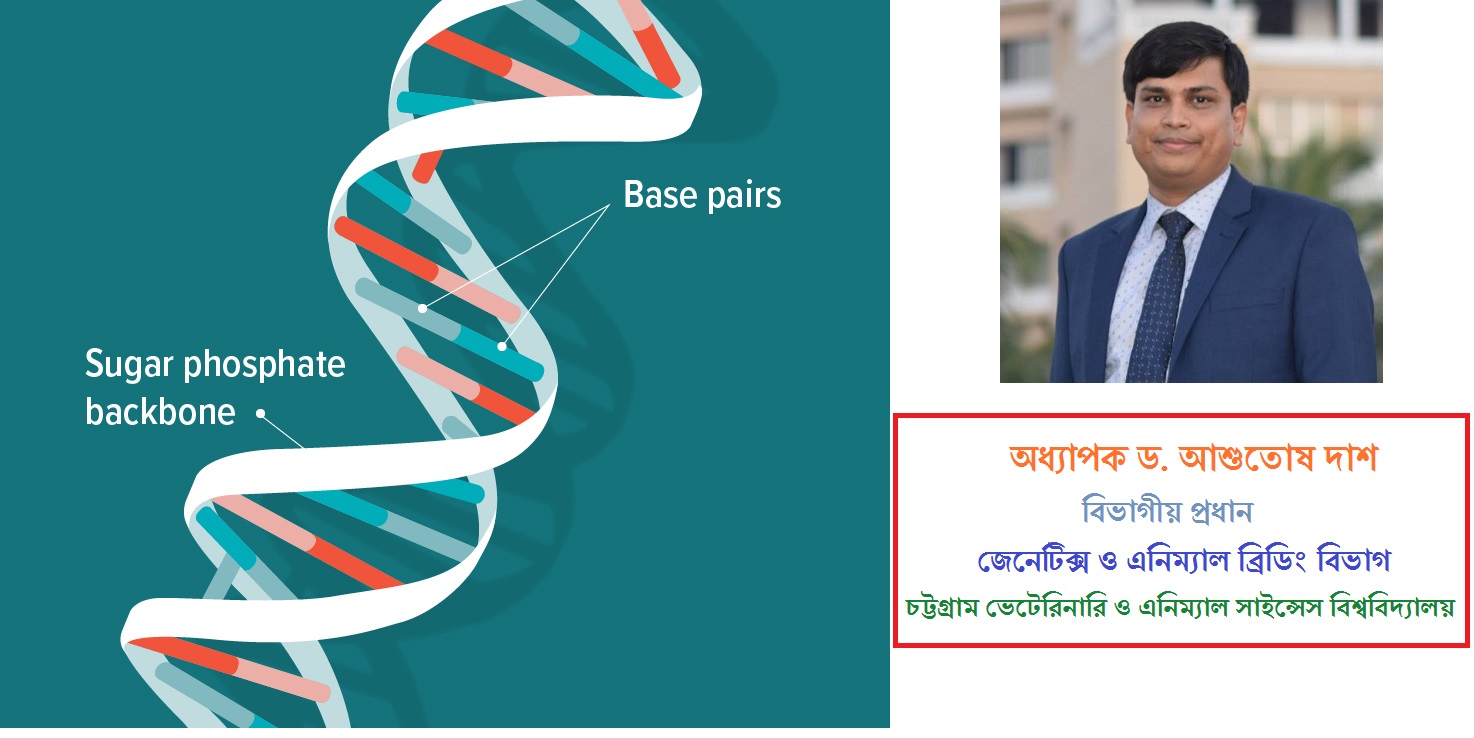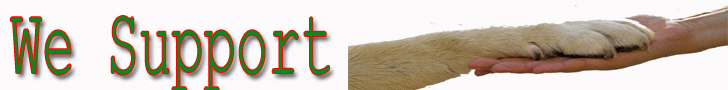করোনায় করুণ পরিণতিতে দেশের পোল্ট্রি শিল্প!
মতামত-ফিচার
পোল্ট্রি খাদ্যের কাঁচামাল, ভ্যাকসিন, মেডিসিন, এন্টিবায়োটিক এবং পোল্ট্রি শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রসহ সকল ধরণের আমদানিকৃত পণ্যের লাগামহীন মূল্য বৃদ্ধির কবলে দেশের পোল্ট্রি শিল্প। অপর দিকে পোল্ট্রি শিল্পে উৎপাদিত পণ্য যেমন একদিন বয়সী ব্রয়লার, লেয়ার ও সোনালী বাচ্চার দামে ধস নেমেছে। ধস নেমেছে ব্রয়লার, সোনালী মুরগীর দামেও। ডিমের দাম এখন কিছুটা ভালো থাকলেও গত দেড় বছরের গড় হিসাব করলে ফলাফল ধসের দিকেই যাবে।
ইতোমধ্যে দেশে মাঝারী ও ছোট হ্যাচারীগুলোর প্রায় ৭০% বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ কেউ আবার ক্যাপাসিটির অর্ধেক, তিনের এক অংশ, চারের এক অংশ চালিয়ে কোনভাবে টিকে আছে। একইভাবে ব্রয়লার ও সোনালী খামারীরাও তাদের লোকসানের পাল্লা ভারী করতে করতে ব্যাংক ও ডিলারের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে বসে আছে।
পোল্ট্রি শিল্পের খাদ্য প্রস্তুতকারী ছোট ও মাঝারী ফিডমিলগুলি প্রতিযোগিতায় বড় ফিড মিলারদের সাথে পেরে উঠছেনা। খাদ্যপণ্যের কাঁচা মালের দাম যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তার তুলনায় খাদ্যের দাম তেমন বাড়েনি। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে করোনা শুরুর আগে ও পরে কাঁচা মালের দাম বেড়েছে প্রায় ৪০-৪৫%, সে তুলনায় খাদ্যের দাম বেড়েছে ১৫% এর মতো। ফলে এখনও ফিড মিলগুলো লোকসান দিয়ে খাদ্য তৈরী করছে। এতে বড় ফিডমিলগুলো টিকলেও অনেক ছোট ও মাঝারী ফিডমিলগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন। এদের অনেকেই উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে।
এই শিল্পে বিনিয়োগকারী প্রায় সকলের দেনার দায় হু হু করে বাড়ছে। ভেঙ্গে পড়েছে গ্রামীন অর্থনীতি। লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষ বেকার হচ্ছে। এভাবেই চলছে করোনার শুরু থেকে এখন পর্যন্ত। বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে এক ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছে এই শিল্পে। মনে হচ্ছে এখানে দেখার কেউ নাই । হাল ও মাঝিবিহীন ঝড়ের কবলে টালমাটাল এক নৌকার মতোই এই শিল্পের অবস্থা।
এই যখন অবস্থা তখন সমস্যার মূলে না গিয়ে আমরা এক পক্ষ আরেক পক্ষকে দোষারোপ করে প্রকৃতপক্ষে নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করে চলেছি । এই সময়ে এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে বিএবি, ফিআব, আহকাব, বাফিটা, বিপিআইএসহ সকল সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এক গোলটেবিল আলোচনার মাধ্যমে সম্ভাব্য করণীয় নিয়ে একটা খসড়া তৈরী করে তা সরকারি মহলে উপস্থাপন করা এবং সকলের স্বার্থে তা বাস্তবায়ন করা অতীব জরুরী হয়ে পড়েছে।
এখন এক নজরে দেখি পোল্ট্রি শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল, রেডি ফিড, প্রিমিক্স, ঔষধ ও ভ্যাকসিনের লাগামহীন মূল্য বৃদ্ধির কারনগুলো-
১। পোল্ট্রি খাদ্যের প্রধান কাঁচামাল ভূট্টা। এই ভূট্টা যা দরকার তার অর্ধেকেরও বেশী আমদানি করতে হয়। কোভিডকালিন সময়ে সারা বিশ্বব্যাপী ভূট্টা উৎপাদন ব্যহত হয়েছে। উৎপাদন খরচও বেড়েছে। এগুলো সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, আমদানি-রপ্তানি খরচও বেড়েছে। ফলে সহসা এর সমাধান হবে এমনটা ভাবা ঠিক হবে না।
২। পোল্ট্রি খাদ্যে ব্যবহৃত ২য় সর্বোচ্চ কাঁচামাল হলো সয়াবিন মিল। এই সয়াবিন মিলের কাঁচামাল সয়াবিন হলো আমদানির উপর নির্ভরশীল। ভূট্টার মতোই সয়াবিনেরও উৎপাদন কমেছে এবং খরচও অনেকগুণ বেড়েছে।
৩। প্রোটিন কনসেন্ট্রেট বা পোল্ট্রি মিল – পোল্ট্রি খাদ্যে ব্যবহৃত একটি গুরুত্বপূর্ন উপাদান। আমদানি নীতিমালায় মিট এন্ড বোন মিল নিষিদ্ধ থাকায় বা কড়াকড়ি আরোপ করায় ফিসমিল ও পোল্ট্রি মিলের উপর চাপ পড়েছে ফলে এগুলোর দাম অনেক বেড়ে গেছে। বন্দরে কাষ্টম জটিলতা, কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর কারনে বন্দর সমূহে নানান সমস্যা, টেস্টে দীর্ঘসূত্রতা ইত্যাদি এই সংকটকে আরও ঘণিভুত করেছে । নানান ধরণের টেস্ট, হয়রানি, বিড়ম্বনা, দেন-দরবার ইত্যাদি কারণে আমদানীকারকরাও এসব জটিলতা এবং বন্দরের ড্যামারেজ দিয়ে প্রোটিন কনসেন্ট্রেড এর এলসি খুলতে চাচ্ছে না। ফলে খাদ্য তৈরীর কাঁচামালের দাম অসহনীয় পর্যায়ে চলে গেছে।
৪। রাইশ পলিশ, ডিওআরবি, ডিডিজিএস, ডিডিজি, ফুলফ্যাট সয়া, সয়াবিন তেল, লাইমস্টোন, ডিসিপি, এমসিপিসহ সকল প্রকার পণ্যের দাম ২০-৪০% পর্যন্ত বেড়েছে।
৫। কোভিডের কারণে বিশ্বব্যাপী পোল্ট্রি খাদ্যে ব্যবহৃত ভিটামিন, মিনারেল, মিথিওনিন, লাইসিন, অন্যান্য এমাইনো এসিড, টক্সিন বাইন্ডার, এসিডিফায়ার, এনজাইম, পিলেট বাইন্ডার, ফাইটোবায়োটিক,কক্সিডিওস্ট্যাট, এন্টিঅক্সিডেন্ট সহ সকল পন্যের কাঁচামালের সংকট দেখা দিয়েছে। অনেক ফ্যাক্টরী শাটডাউন-লকডাউন এর কারনে দীর্ঘদিন বন্ধ রয়েছে। যেগুলো চালু আছে সেগুলিও অল্প সংখ্যক জনবল দিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে উৎপাদন কমেছে এবং সমান তালে উৎপাদন খরচও বেড়েছে। এগুলোর মূল্য করোনার আগের চেয়ে বর্তমানে প্রায় ২৫-৪৫% এবং কিছু কিছু আইটেম ১০০-১৫০% পর্যন্ত বেড়েছে।
৬। পোল্ট্রিতে সরাসরি ব্যবহৃত ভ্যাকসিন, ঔষধ সমূহ, ইকুইপমেন্টস ইত্যাদি পণ্যের কাঁচামালের দামও প্রায় ৩০-৫০% পর্যন্ত বেড়েছে। অনেক কাঁচামাল উৎপাদনকারী ফ্যাক্টরী শাটডাউন-লকডাউন এর কারণে বন্ধ রয়েছে।
৭। আমদানি খরচ বেড়েছে, কনটেইনার এর ভাড়া বেড়েছে। ২০ ফিট কনটেইনার ইউরোপ থেকে আসতো ১৫০০-২০০০ ডলারে,এই ভাড়া এখন বেড়ে ২৫০০-৩০০০ ডলার হয়েছে। একই সাথে বন্দরে কনটেইনার জটে শিপিং ড্যামারেজ, পোর্ট ড্যামারেজ গুণতে হচ্ছে। দেশে বেড়েছে পরিবহন ভাড়াও। করোনার কারণে সঠিক সময়ে মাল পৌঁছতে বিলম্ব হচ্ছে, ফলে বাজারে পণ্যের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে।
৮। সকল ধরণের প্লাস্টিক পণ্য, লৌহজাত পণ্য, স্টীল ইত্যাদি পোল্ট্রি সংশ্লিষ্ট পন্যের দাম ২০-৩০% পর্যন্ত বেড়েছে।
৯। ফিডমিলের আমদানিকৃত সকল যন্ত্রপাতির মূল্য বহুগুণে বেড়েছে।
১০। ব্যাংকগুলো সময় মতো অর্থ ছাড়করনের ক্ষেত্রে গড়িমসি করছে। ক্ষেত্র বিশেষ পাস হওয়া লোনের অর্থ ছাড় করছে না। আবার কেউ নতুন করে লোন করতেও পারছে না। অনেক ব্যাংক করোনার কারনে সঠিক সময়ে এলসি খুলতে পারছে না। লেনদেন সীমিত হওয়াতে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে এই শিল্পে।
১১। করোনার কারনে বিভিন্ন নিরব খরচগুলো আগের তুলনায় অনেক গুণে বেড়েছে।
১২। কোভিডকালিন সময়ে ডিএলএস এর এনওসি দেরীতে দেওয়ার কারনেও পন্যের উপর অতিরিক্ত খরচ যোগ হচ্ছে।
১৩। ডলার ও ইউরোর রেটও বেড়েছে।
১৪। ইউরোপ, আমেরিকা, চায়না সহ বিভিন্ন দেশ হতে পন্য আসতে দেরী হওয়ায় ব্যাংকের ইন্টারেস্ট বৃদ্ধি পাচ্ছে।
১৫। পোল্ট্রিতে ব্যবহৃত জীবন রক্ষাকারী ঔষধ এন্টিবায়োটিক সমূহের মূল্য করোনার আগের তুলনায় বর্তমানে প্রায় ২০-৫০% পর্যন্ত বেড়েছে ।
এবার চলুন দেশে উৎপাদিত প্যারেন্টস্টক বাচ্চা, লেয়ার, ব্রয়লার ও সোনালীর বাচ্চা, ব্রয়লার ও সোনালী মুরগি এবং ডিমের দাম কমে যাওয়ার কারনগুলো বের করার চেষ্টা করি-
১। দেশের ১৩ টি ব্রয়লার জিপি ফার্ম থেকে ব্রয়লার প্যারেন্টস চাহিদার তুলনায় অনেক বেশী উৎপাদিত হচ্ছে। দেশে কি পরিমান ব্রয়লার প্যারেন্ট এবং কি পরিমান একদিন বয়সী ব্রয়লার বাচ্চা দরকার এর কোন স্টাডি না থাকায় জিপি আনার ক্ষেত্রে কোন নীতিমালা নাই। ফলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিপি আসছে । এর পরেও কেউ কেউ আবার দেশের বাইরে থেকেও আনছেন। এই অতিরিক্ত জিপি থেকে অতিরিক্ত পিএস বের হচ্ছে। অনেক সময় এই পিএস বাচ্চাগুলো অতি অল্প মূল্যে ব্রীডার ফার্মগুলোতে সেল হচ্ছে,। সেল করতে না পেরে অনেকেই নিজেদের ক্যাপাসিটি বাড়াচ্ছেন। আবার কেউ কেউ দাম কম থাকায় বা সেল করতে না পেরে কমার্শিয়াল ব্রয়লার বাচ্চা হিসেবে সেল করছেন। এর ফলে প্যারেন্টস বাচ্চা সেলের ক্ষেত্রে জিপি ফার্ম মালিকদের প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে।
২। দেশে ব্রয়লার প্যারেন্টস্টক এর পরিমানও চাহিদার তুলনায় অনেক বেশী ফলে ব্রয়লার বাচ্চার উৎপাদনও অনেক বেশী। ব্রয়লার বাচ্চার উৎপাদন খরচ ২৮-৩২ টাকা হলেও গত ২ বছর যাবত গড়ে ১৮-২০ টাকা করে বিক্রয় হচ্ছে। ক্ষতির পরিমান সহজেই অনুমান করা যায়।
৩। লেয়ার প্যারেন্টস এর অবস্থাও একই রকম। একদিন বয়সী লেয়ার বাচ্চার উৎপাদন অনেক বেশী। হ্যাচারীতে একদিন বয়সী লেয়ার বাচ্চার বর্তমান উৎপাদন খরচ প্রায় ৩০-৩৫ টাকা কিন্তু গত দেড় বছর যাবত বিক্রি হচ্ছে ২০-২৫ টাকা করে। এখানেও হ্যাচারী মালিকদের ক্ষতির পরিমান বিরাট অংকের।
৪। দেশে ব্রয়লার ব্রীডারের পাশাপাশি বিগত কয়েক বছরে সোনালী জাতের প্যারেন্টস্টক ফার্ম ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে । অনেক বড় বড় হ্যাচারীতেও এখন কালার ব্রয়লার এমনকি সোনালী জাতের বাচ্চাও উৎপাদন করছে। এগুলোর দামও গত ২ বছরে গড়ে ১০-১২ টাকা করে বিক্রয় হচ্ছে। এখানেও হ্যাচারী মালিকদের অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে।
৫। বাণিজ্যিক ব্রয়লার মুরগি ৮৫-১০৫ টাকা কেজি হিসেবে বিক্রয় হচ্ছে। যার উৎপাদন খরচ এখন কেজি প্রতি প্রায় ১০৫ টাকা চেয়ে বেশী। সোনালী চিকেন ১৩০-১৫০ টাকায় বিক্রয় হচ্ছে যা উৎপাদন খরচের চেয়ে অনেক কম। এর সাথে রিজেক্ট লেয়ার প্যারেন্টস, রিজেক্ট লেয়ার, রিজেক্ট ব্রয়লার প্যারেন্টস, রিজেক্ট সোনালী প্যারেন্টসও প্রচুর মার্কেটে।
৬। ডিমের দাম দীর্ঘদিন প্রতিটি ৪-৫ টাকা ছিল, সম্প্রতি একটু দাম বেড়েছে। তবে খাদ্যের দাম তুলনা করলে এখানেও মূলধন নিয়ে টানাটানি অবস্থা। করোনাকালিন সময় হিসেব করলে গড়ে প্রতিটি ডিমের উৎপাদন খরচ ৬.৫০ টাকার চেয়ে বেশী। আর বর্তমান সময়ের খরচ হিসেব করলে তা হবে ৭.৫০ টাকার মতো।
৭। এর পাশাপাশি ব্রয়লার প্যারেন্টস, লেয়ার প্যারেন্টস, লেয়ার এবং সোনালী সহ প্রায় সকল মুরগিতে এইচ৫, এইচ৭, এইচ৯ সহ নানা জটিল রোগে ১৫-২০% মুরগি মারা যায় যার হিসেব টানলে সকল উৎপাদিত পণ্যের উপর আরও ১৫-২০% উৎপাদন খরচ বেশী হবে।
এখন দেখা যাক উৎপাদিত ব্রয়লার, সোনালী, লেয়ার, ডিমের দাম দীর্ঘদিন যাবত কম থাকার মূল কারন হলো – কোভিড১৯ বা করোনা –
১। করোনার কারনে হোটেল, রেস্তোরা, শপিংমল, পর্যটন এলাকাগুলো দীর্ঘদিন যাবত প্রায় বন্ধ বললেই চলে। কিছু সময় চললেও লোকজন খুবই কম। এগুলোতে অবস্থিত ক্যাফে, হোটেল গুলোতে ডিম, মুরগিই ছিল প্রধান আইটেম।
২। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার কারনে সেখানকার হোটেল, রেস্টুরেন্ট, ডাইনিং বন্ধ। স্কুলের পিকনিক, শিক্ষা সফর, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, রাজনৈতিক কর্মকান্ড, গেটটুগেদর, এলামনাই, রি-ইউনিয়ন, সামাজিক কর্মকান্ড, খেলা-ধুলা বন্ধ থাকায় এখানে আর ব্রয়লার, চিকেন, ডিম লাগে না।
৩। স্থানীয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বন্ধ। এই সকল অনুষ্ঠানে ডিম, মুরগিই ছিল প্রধান খাবার।
৪। বিয়ে-সাদী, জন্মদিন, বিভিন্ন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, খেলা-ধুলা, ধর্মীয় উৎসবে আগের মতো আর লোকজনের যাওয়া আসা নাই। এগুলো অনুষ্ঠানে প্রচুর ডিম, মুরগি লাগতো।
৫। দেশে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, মিছিল, মিটিং বন্ধ আছে। এখানেও অনেক মুরগি, ডিম লাগতো।
৬। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সেক্টরের বছর ব্যাপী কোন না কোন এক্সিবিশন/মেলা হতো যা করোনার পর থেকে বন্ধ আছে। এখানে প্রচুর ডিম ও মুরগি লাগতো।
৭। বিমানের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফ্লাইটগুলো বন্ধ আছে। বিমান বন্দরে, বিমানের খাবারে চিকেন একটা কমন আইটেম যা এখন আর লাগে না।
৮। বিস্কুট, চিপস, ফাস্ট ফুড উৎপাদনে এখন আর আগের মতো চিকেন আর ডিম লাগে না কারন এগুলোর চাহিদা কমে গেছে।
৯। নতুন নতুন ফ্যাক্টরী স্থাপন, সিভিল কার্যক্রম, ইন্সটলমেন্টের কাজ অনেক কমে গেছে।
১০। করোনার কারনে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা অনেক কমে গেছে। লকডাউনের কারনে অনেকের আয় নাই বললেই চলে। অনেকেই পূর্বের জমানো অর্থ থেকে খুব হিসাব নিকাশ করে চলছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু প্রতিষ্ঠান তাদের জনবল কাটসাট করেছে এবং নতুন কোন নিয়োগ না হওয়াতে বেকারের সংখ্যা আশংকা জনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমতাবস্থায় মানুষ তার চাহিদার তুলনায় অনেক কম খরচে চলার চেষ্টা করছে।
১১। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া গুলোতে তেমন একটা প্রচার প্রচারনা নাই। কোভিড প্রতিরোধে চিকেন ও ডিমের কোন বিকল্প নাই এই বিষয়টি আমাদের মন্ত্রনালয়ের পাশাপাশি স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়ের ডাক্তার, পুষ্টিবিদদের মাধ্যমে ব্যাপক ভাবে প্রচারনার অভাব।
এই সকল কারনগুলো ছাড়াও আরও অনেক মিথ্যা ও বানোয়াট কাহিনি সাজিয়ে ভোক্তাদের বিভ্রান্তিতে ফেলে প্রায়শই আমাদের এই শিল্পকে ক্ষতির মুখে ফেলে দেয়।
আমি এতোক্ষণ ধরে যা বকবক করে লিখলাম তা কম বেশী সকলেরই জানা আছে, তবে আমাদের সাধারন ভোক্তা এবং প্রান্তিক পর্যায়ে খামারীদের নজরে এ বিষয়গুলো পৌঁছাতে পারলে অন্তত তারা জানতে পারবে আসল বিষয়টা কি । অতীব দুঃখের বিষয় হলেও সত্যি আমার এই লেখা আমাদের লোকজন ছাড়া সাধারন মানুষ ও ভোক্তাদের কাছে পৌছঁবেনা।
এখানে একটা বিষয় পরিস্কার করা দরকার- বড় বড় হ্যাচারী/ব্রীডার ফার্ম/ফিডমিলার মিলে গোটা বিশেক প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের পরিমান টোটাল বিনিয়োগের প্রায় অর্ধেক। তারা নিজেদের প্যারেন্ট, নিজেদের লেয়ার, নিজেদের ব্রয়লার, নিজেদের ফিড নিজেরাই ব্যবহার করে এবং উৎপাদিত ডিম, মুরগি সরাসরি বিপননের ব্যবস্থা করে থাকে। ফলে তাদের সাথে মাঝারী ও ছোট হ্যাচারী,ফার্ম, ফিডমিলারগন কখনও পেরে উঠবে না। একজন বড় ফিডমিলার সিজনের সময় প্রায় ৬-৭ মাসের ভূট্টা, সয়াবিন কিনে রাখেন। কাজেই তাদের সাথে তুলনা দিয়ে কোন লাভ নেই।
তবে এসোসিয়েশনগুলো চাইলে, সরকারের সহযোগীতা নিয়ে দেশের মানুষের আয় ও ক্রয় ক্ষমতা চিন্তা করে জিপি, পিএস এবং ব্রয়লার, লেয়ার ও সোনালীর চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন ও বিপননের ব্যবস্থা করতে পারলে হয়তোবা করোনা উত্তর সময়ে টিকে থাকা সম্ভব হবে। অন্যথায় বিরাট একটি অংশ মূলধন খুইয়ে ফকির হবে। অপর দিকে গুটি কতক প্রতিষ্ঠানের মালিকগন আমির হয়ে যাবে।
আমার দেখা গত ১৮ বছরে দেশের হাজার হাজার খামার মালিক তাদের ব্যবসা যেমন গুটিয়ে নিয়েছে ঠিক তেমনিভাবে দেশী বিদেশী বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান তাদের বিনিয়োগ বাড়িয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে যে পরিমান লেয়ার প্যারেন্ট, লেয়ার মুরগি, ব্রয়লার প্যারেন্ট, সোনালী প্যারেন্ট বিক্রি হয়ে গেছে তাতে আগামী ২/৩ মাস যারা টিকে থাকবে তারা ঠিকই ক্ষতিটা পুষিয়ে নিতে পারবে। একই ঘটনা ফিড মিলগুলোর বেলায়ও। তখন নতুন আরেকটা শ্রেণি আসবে যারা রাতারাতি লাভ করে বড় হওয়ার চিন্তায় বিভোর থাকবে। কিন্তু আখেরে তাদের পরিণতিও একই রকম হবে। অর্থাৎ একটা শ্রেণি সব সময় টিকে থাকবে এবং ধীরে ধীরে তারা এক সময় দেশে সমস্ত মুরগির খাদ্য, ডিম, মুরগি উৎপাদন করবে এবং একচেটিয়া সেক্টর নিয়ন্ত্রন করবে। আরেকটা শ্রেণি নগদ লাভ নামক মরীচিকার আশায় পালা বদল করতে থাকবে।
ঔষধ কোম্পানীর বেলায়ও একই অবস্থা হবে। আমাদের সরকারগুলোর ভূমিকা হলো আমার আম ছালা দুইই চাই। উৎপাদনও বেশী চাই এবং জনগনকে সস্তায় খাওয়াতেও চাই। আর উৎপাদনতো কেউ না কেউ করবেই। মরে হোক আর বেঁচে হোক। সব মিলিয়ে সেক্টরের অবস্থা ভালো বলতে পারা খুব কঠিন ।
আমি বিশ্বাস করতে চাই না যে, আমার এই লেখা দিয়ে শীর্ষ মহলের টনক নড়ানো যাবে কিংবা নড়বে। আমি নড়াতেও চাই না। আমাকে গত ১ মাস ধরে বেশ কিছু প্রিয় মানুষ ফোন করে এই শিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কি জানতে চাওয়ায় তাদের জন্যই এই লেখাটা। এই কঠিন অবস্থা থেকে খুব সহসা আমরা বের হতে পারবো এমনটা প্রত্যাশা করা কঠিন। তবে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ ভাবে নিজেদের শিল্পকে স্থানীয়ভাবে এবং করপোরেট পর্যায়ে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনে জাতীয়ভাবে কিছু বাস্তব এবং কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়া যায় তাহলে হয়তো করোনা উত্তর পৃথিবীতে আমরা সকলে টিকে থাকতে পারবো।
তাই বলতে পারি – করোনায় করুণ পরিণতিতে দেশের পোল্ট্রি শিল্প।
বেশী বেশী ডিম ও মুরগি খান
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ান।
ভালো থাকুন, নিরাপদে থাকুন।
মাস্ক পড়ুন, টিকা নিন।
করোনা থেকে মুক্ত থাকুন।
লেখক :
ডাঃ মোহাম্মদ সরোয়ার জাহান
ন্যাশনাল পোল্ট্রি কনসালটেন্ট ও
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সেইফ বায়ো প্রোডাক্টস্ লিঃ